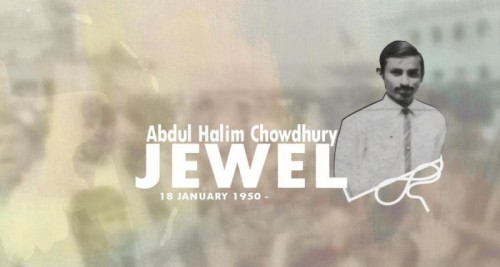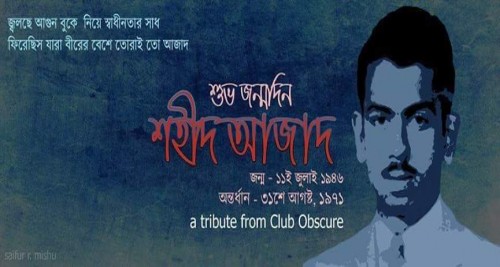পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বা সোমপুর বিহার বা সোমপুর মহাবিহার বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। পালবংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপাল দেব (৭৮১-৮২১) অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকে এই বিহার তৈরি করছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এই বিশাল স্থাপনা আবিষ্কার করেন।
পাহাড়পুরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৌদ্ধবিহার বলা যেতে পারে। আয়তনে এর সাথে ভারতের নালন্দা মহাবিহারের তুলনা হতে পারে। এটি ৩০০ বছর ধরে বৌদ্ধদের অতি বিখ্যাত ধর্ম শিক্ষাদান কেন্দ্র ছিল। শুধু উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকেই শুধু নয়, চীন, তিব্বত, মায়ানমার (তদানীন্তন ব্রহ্মদেশ), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা এখানে ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে আসতেন। খ্রিস্টীয় দশম শতকে বিহারের আচার্য ছিলে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের স্বীকৃতি প্রদান করে।
অবস্থান ও আয়তন
পুন্ড্রবর্ধনের রাজধানী পুন্ড্রনগর (বর্তমান মহাস্থান) এবং অপর শহর কোটিবর্ষ (বর্তমান বানগড়)-এর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত ছিল সোমপুর মহাবিহার। এর ধ্বংসাবশেষটি বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহীর অন্তর্গত নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। অপরদিকে জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে এর দূরত্ব পশ্চিমদিকে মাত্র ৫ কিলোমিটার। এর ভৌগোলিক অবস্থান ২৫°০´ উত্তর থেকে ২৫°১৫´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫০´ পূর্ব থেকে ৮৯°১০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত। গ্রামের মধ্যে প্রায় ০.১০ বর্গ কিলোমিটার (১০ হেক্টর) অঞ্চল জুড়ে এই পুরাকীর্তিটি অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক এই নিদর্শনটির ভূমি পরিকল্পনা চতুর্ভূজ আকৃতির। এটি বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের প্লাবন সমভূমিতে অবস্থিত, প্লাইস্টোসীন যুগের বরেন্দ্র নামক অনুচ্চ এলাকার অন্তর্ভুক্ত। মাটিতে লৌহজাত পদার্থের উপস্থিতির কারণে মাটি লালচে। অবশ্য বর্তমানে এ মাটি অধিকাংশ স্থানে পললের নিচে ঢাকা পড়েছে। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৩০.৩০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত পাহাড়সদৃশ স্থাপনা হিসেবে এটি টিকে রয়েছে। স্থানীয় লোকজন একে গোপাল চিতার পাহাড় আখ্যায়িত করত; সেই থেকেই এর নাম হয়েছে পাহাড়পুর, যদিও এর প্রকৃত নাম সোমপুর বিহার।
আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট
ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমনের পর তাঁরা সকল স্থানে জরিপ কাজ চালানো শুরু করেন। পূর্ব ভারতে জরিপ কাজ পরিচালনা করেন বুকানন হ্যামিল্টন; যিনি ১৮০৭ থেকে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে পাহাড়পুর পরিদর্শন করেন। এটিই ছিল পাহাড়পুরে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক পরিদর্শন। এরপর এই প্রত্নস্থল পরিদর্শনে আসেন ওয়েস্টম্যাকট। এঁরা দেশে ফিরে তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্বলিত বিবরণ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এরই সূত্র ধরে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার কানিংহাম এই ঐতিহাসিক স্থানটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের পর এই জমিটি ব্যাপক হারে খনন করার প্রতি তিনি আগ্রহ দেখান। কিন্তু জমির মালিক বলিহারের তদানীন্তন জমিদার তাঁকে এই কাজে বাধা দেন। তাই তিনি বিহার এলাকার সামান্য অংশে এবং পুরাকীর্তির কেন্দ্রীয় ঢিবির শীর্ষভাগের সামান্য অংশে খনন কাজ চালিয়েই অব্যাহতি দেন। এই খননকার্যের সময় কেন্দ্রীয় ঢিবির অংশে চারপাশে উদ্গত অংশবিশিষ্ট একটি বর্গাকার ইমারত আবিষ্কার করেন যার দৈর্ঘ্য ছিল ২২ ফুট। অবশেষে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের প্রত্নতাত্ত্বিক আইনের আওতায় এই স্থান ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসাবে ঘোষিত হয়।
ইতিহাস ও পটভূমি
৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে হিউয়েন ৎসাং পুন্ড্রবর্ধনে আসেন, তবে তার বিস্তারিত বিবরণে সোমপুরের বিহার ও মন্দিরের কোন উল্লেখ নেই। গোপালের পুত্র ধর্ম পাল (৭৮১ - ৮২২ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন ও রাজ্যকে বাংলা বিহার ছাড়িয়ে পাকিস্তানের উত্তর - পশ্চিম সীমান্তের গান্ধার পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। সম্রাট ধর্মপাল অনেক নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন ও তিনিই বিক্রমশীলা ও সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। অন্য মতে, বিখ্যাত তিব্বতীয় ইতিহাস গ্রন্থ "পাগ সাম জোন ঝাং" এর লেখক অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (৮১০-৮৫০) কর্তৃক সোমপুরে নির্মিত বিশাল বিহার ও সুউচ্চ মন্দিরের উল্লেখ করেছেন। সোমপুর বিহারের ভিক্ষুরা নালন্দা, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি ভারতীয় বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থস্থানে অর্থ ও ধন রত্ন দান করতেন বলে বিভিন্ন লিপিতে উল্লেখ করা আছে, যা ১০ম - ১১শ শতাব্দীতে সমৃদ্ধশীল অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়া ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সোমপুর বিহার ছাড়াও অগ্রপুর (রাজশাহীর অগ্রাদিগুণ), উষ্মপুর, গোটপুর, এতপুর ও জগদ্দল ( রাজশাহীর জগদল) বিহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে গুর্জর রাজ প্রথম ভোজ ও মহেন্দ্র পাল, পাল সাম্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতিসাধন করেন। পরে ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে পাল বংশীয় রাজা মহীপাল (৯৯৫ - ১০৪৩) সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন ও সোমপুর বিহার মেরামত করেন। কিন্তু মহীপাল ও তার পুত্র নয়াপালের মৃত্যুর পর আবার পাল বংশের পতন শুরু হয়। এই সুযোগে মধ্যভারতের চেদীরাজ কর্ণ, চোলরাজ রাজেন্দ্র ও দিব্বো নামের এক দেশীয় কৈবর্ত সামন্ত নরপতি পর পর বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করেন। নালন্দায় পাহাড়পুর মন্দির ও বিহার ধ্বংসের উল্লেখ সম্ভবত এ সময়ের আক্রমণের। ১১শ শতাব্দীতে পাল বংশীয় রামপাল হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ১২শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট থেকে আগত সেন রাজারা বাংলা দখল করেন। সে রাজদের আমলে সোমপুর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারায়। এ সময় শেষবারের মত সোমপুরের পতন শুরু হয়। ১৩শ শতাব্দীর শুরুতে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ - বিন - বখতিয়ার খিলজী বাংলায় আক্রমণ করে উত্তরবঙ্গের বৃহদাংশ দখল করে নেন। সম্ভবত এই মুসলমান শাসকদের মূর্তিবিরোধী মনোভাবের ফলেই বৌদ্ধদের এই বিহার ও মন্দির সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যায়।
প্রত্নতাত্ত্বিক খনন
পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্বকালীন সময়ে মূলত বৃটিশ যুগে, এবং দ্বিতীয়ত স্বাধীনতা-উত্তর কালে আশির দশকে। ১৮৭৯ সালে কানিংহাম প্রথম উদ্যোগটি নেন। কিন্তু বলিহারের জমিদারের বিরোধিতায় কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ঢিবির শীর্ষভাগ খনন করে তাঁকে থেমে যেতে হয়। এ খননে চারপাশে উদগত অংশযুক্ত প্রায় ৭মি উঁচু একটি কক্ষ আবিষ্কৃত হয়। এর দীর্ঘদিন পর ১৯২৩ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র গবেষণা পরিষদ ও ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টায় এবং দিঘাপতিয়ার জমিদার পরিবারের সদস্য শরৎ কুমার রায়ের অর্থানুকূল্যে পুনরায় খননকাজ শুরু হয়। এ বছর ঐতিহাসিক ডি.আর.ভান্ডারকরের নেতৃত্বে প্রত্নস্থলটির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে খনন পরিচালিত হলে উত্তর-দক্ষিণে বিন্যস্ত একসারি কক্ষ এবং চত্বরের অংশবিশেষ পাওয়া যায়। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ১৯২৫-২৬ সালে খনন করে কেন্দ্রীয় ঢিবির উত্তরে প্রধান সিঁড়ি, পোড়ামাটির ফলকচিত্র শোভিত দেয়াল ও প্রদক্ষিণ পথসহ উত্তর দিকের মন্ডপ বা হল ঘর আবিষ্কার করেন। ফলে প্রথমবারের মত এ বিহারের ভূমিপরিকল্পনা ও দেয়ালচিত্রণ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৩০-৩১ এবং ১৯৩১-৩২ সালে জি.সি.চন্দ্র বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ও সংলগ্ন চত্বর খনন করেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে কাশিনাথ দীক্ষিতের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ পুনরায় খনন করে। এতে বিহার ও মন্দিরের অবশিষ্ট অংশ এবং সত্যপীরের ভিটায় একগুচ্ছ স্তূপসহ একটি তারা মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রফিক মোঘল পূর্ব বাহুর কয়েকটি কক্ষে গভীর উৎখনন পরিচালনা করেন।
স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ১৯৮১-৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ 'নতুন তথ্যের অনুসন্ধান এবং ইতোপূর্বে দীক্ষিতের আবিষ্কৃত কক্ষসমূহের প্রাপ্ত নিদর্শনাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া'র উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের খনন কাজ শুরু করে। ১৯৮৭-৮৯ সালে পুনরায় খনন পরিচালিত হয় বিহার অঙ্গন থেকে অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল ও পূর্ববর্তী খননের স্তূপীকৃত মাটি অপসারণ করে সুশৃঙ্খল পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যেন বিহারে বিদ্যমান জলাবদ্ধতা দূরীভূত হয় এবং লবণাক্ততা হ্রাস পায়।
স্থাবর স্থাপত্য নিদর্শনসমূহ
বিহার
বৌদ্ধ বিহারটির ভূমি-পরিকল্পনা চতুষ্কোনাকার। উত্তর ও দক্ষিণ বাহুদ্বয় প্রতিটি ২৭৩.৭ মি এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাহুদ্বয় ২৭৪.১৫ মি। এর চারদিক চওড়া সীমানা দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। সীমানা দেয়াল বরাবর অভ্যন্তর ভাগে সারিবদ্ধ ছোট ছোট কক্ষ ছিল। উত্তর দিকের বাহুতে ৪৫টি এবং অন্য তিন দিকের বাহুতে রয়েছে ৪৪টি করে কক্ষ। এই কক্ষগুলোর তিনটি মেঝে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি মেঝে বিছানো ইঁটের ওপর পুরু সুরকী দিয়ে অত্যন্ত মজবুত ভাবে তৈরি করা হয়েছিলো। সর্বশেষ যুগে ৯২টি কক্ষে মেঝের ওপর বিভিন্ন আকারের বেদী নির্মাণ করা হয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রথম যুগে সবগুলো কক্ষই ভিক্ষুদের আবাসকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীকালে কিছু কক্ষ প্রার্থনাকক্ষে রুপান্তর করা হয়েছিলো।
কক্ষগুলোর প্রতিটিতে দরজা আছে। এই দরজাগুলো ভেতরের দিকে প্রশস্ত কিন্তু বাইরের দিকে সরু হয়ে গেছে। কোন কোন কক্ষে কুলুঙ্গি পাওয়া যায়। কুলুঙ্গি সম্বলিত কক্ষগুলোর মেঝেতে দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য বেশ কিছু দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। ভেতরের দিকে কক্ষগুলোর দৈর্ঘ্য ৪.২৬ মি এবং প্রস্থ ৪.১১ মি। কক্ষের পেছনের দিকের দেয়াল অর্থাৎ সীমানা দেয়াল ৪.৮৭মি এবং সামনের দেয়াল ২.৪৪মি চওড়া। কক্ষগুলোর সামনে ২.৫ মি. প্রশস্ত টানা বারান্দা আছে। ভেতরের দিকের উন্মুক্ত চত্বরের সাথে প্রতিটি বাহু সিঁড়ি দিয়ে যুক্ত।
বিহারের উত্তর বাহুর মাঝ বরাবর রয়েছে প্রধান ফটক। এর বাইরের ও ভেতরের দিকে একটি করে স্তম্ভ সংবলিত হলঘর এবং পাশে ছোট ছোট কুঠুরি আছে। এই কুঠুরিগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত। প্রধান ফটক এবং বিহারের উত্তর-পূর্ব কোনের মাঝামাঝি অবস্থানে আরও একটি ছোট প্রবেশ পথ ছিলো। এখান থেকে ভেতরের উন্মুক্ত চত্বরে প্রবেশের জন্য যে সিঁড়ি ব্যবহৃত হত তা আজও বিদ্যমান। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম বাহুতেও অনুরুপ সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিলো। এদের মাঝে কেবল পশ্চিম বাহুর সিঁড়ির চিহ্ন আছে। উত্তর বাহুর প্রবেশ পথের সামনে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত একটি পুকুর ছিল। ১৯৮৪-৮৫ সালের খননে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রথম নির্মাণ যুগের পরবর্তী আমলে এ পুকুর খনন করা হয় এবং এসময় এ অংশের সিঁড়িটি ধ্বংস করে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে পুকুরটি ভরাট করে দেয়া হয়।
কেন্দ্রীয় মন্দির
বিহারের অন্তর্বর্তী স্থানের উন্মুক্ত চত্বরের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ। এখন এটি ২১মি উঁচু হলেও মূল মন্দিরটি কমপক্ষে ৩০ মি উঁচু ছিল। তিনটি ক্রমহ্রাসমান ধাপে ঊর্ধ্বগামী এ মন্দিরের ভূমি-পরিকল্পনা ক্রুশাকার। প্রতিটি ক্রুশবাহুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১০৮.৩ মি ও ৯৫.৪৫মি। কুশের মধ্যবর্তী স্থানে আরও কয়েকটি অতিরিক্ত দেয়াল কৌণিকভাবে যুক্ত। মূল পরিকল্পনাটির কেন্দ্রে দরজা-জানালা বিহীন একটি শূন্যগর্ভ চতুষ্কোণাকার প্রকোষ্ঠ আছে। এই প্রকোষ্ঠটি মন্দিরের তলদেশ থেকে চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। মূলতঃ এ শূন্যগর্ভ প্রকোষ্ঠটিকে কেন্দ্র করেই সুবিশাল এ মন্দিরের কাঠামো নির্মিত। এ কক্ষের চারদিকে মন্দিরের দ্বিতীয় ধাপে চারটি কক্ষ ও মন্ডপ নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলেই মন্দিরটি ক্রুশাকার ধারণ করেছে। মন্দির পরিকল্পনার সমান্তরালে দেয়াল পরিবেষ্টিত প্রদক্ষিণ পথ আছে। অনুরুপভাবে প্রথম ধাপে দ্বিতীয় ধাপের প্রদক্ষিণ পথের দেয়ালের চারদিকে চারটি কক্ষ যুক্ত করে ক্রুশাকৃতি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে এবং এর সমান্তরালে প্রদক্ষিণ পথ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথম ধাপের সমান্তরালে মন্দিরের ভিত্তিভূমির পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। উত্তর দিকের মধ্যবর্তীস্থলে সিঁড়ি ছিল। পরবর্তিতে এ সিঁড়ি ধ্বংস করে তার উপর কিছু নতুন কাঠামো নির্মাণ করা হয়।
কেন্দ্রীয় শূন্যগর্ভ কক্ষে একটি ইঁট বাধানো মেঝে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ মেঝে কক্ষের বাইরে চারদিকের কক্ষ ও মন্ডপের প্রায় একই সমতলে অবস্তথিত। কিন্তু চারদিকের কক্ষগুলো থেকে কেন্দ্রীয় এ কক্ষে যাওয়ার কোন পথ বা দরজা নেই এবং আগে ছিলো,পরে বন্ধ করা হয়েছে এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। কক্ষে মূর্তি রাখার বেদী বা কুলুঙ্গী কিছুই নেই। তাই অনুমিত হয় ফাঁপা এ দন্ডটি মন্দিরের সুউচ্চ দেয়ালগুলোর সুদৃঢ় নির্মানের জন্য একটি উপকরণ ছিল। মূর্তিগুলো সম্ভবত এর চারদিকের কক্ষগুলোতে স্থাপন করা হয়েছিলো। মন্দিরের শীর্ষদেশের কোন নিদর্শন নেই বিধায় এর ছাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কিছু বলা যায় না।
কেন্দ্রীয় শূন্যগর্ভ কক্ষটির দেয়াল নিরাভরণ কিন্তু প্রতিটি ধাপের দেয়ালগুলোর বহির্ভাগ উদগত কার্নিশ, অলংকৃত ইঁট এবং সারিবদ্ধ পোড়ামাটির ফলকচিত্র দ্বারা সজ্জিত। ক্রুশাকার পরিকল্পনার বর্ধিত অংশগুলোর সংযোগস্থলে কার্নিশের প্রান্ত পর্যন্ত পানি নিষ্কাশন নালার ব্যবস্থা আছে। পাথর নির্মিত এ নালাগুলোর মুখ গর্জনরত সিংহের মুখের অবয়বে নির্মিত। ভিত্তিভূমির দেয়ালের বহির্দেশে ৬৩টি কুলুঙ্গি আছে। এর প্রতিটিতে একটি করে পাথরের ভাস্কর্য ছিলো।
উন্মুক্ত অঙ্গন
বিহারের মধ্যবর্তী উন্মুক্ত অঙ্গনে আরও কিছু ইমারতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এদের মাঝে বেশ কিছু ইমারতের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। অঙ্গনের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ভোজনশালা ও রন্ধনশালা অবস্থিত। এ দুটি স্থাপনার মাঝে ৪৬মি দীর্ঘ ইট বাঁধানো একটি নর্দমা আছে এবং এর কাছে এক সারিতে তিনটি কূপ আছে। এছাড়াও রয়েছে কিছু নিবেদন স্তূপ, প্রশাসনিক ভবন, কেন্দ্রীয় মন্দিরের প্রতিকৃতি ইত্যাদি। নিবেদন স্তূপগুলোর মাঝে দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত স্তূপটি ১৬কোণ বিশিষ্ট নক্ষত্র আকৃতির। অনুচ্চ একটি মঞ্চের মাঝে সংস্থাপিত এ স্তূপটির সংলগ্ন স্থানে রয়েছে একটি পাকা কূপ। অন্যান্য নিবেদন স্তূপগুলো বিক্ষিপ্তভাবে নির্মিত। চত্বরের উত্তর-পূর্বাংশের ইমারতগুলো সম্ভবত প্রশাসনিক এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হত।
স্নানাগার ও শৌচাগার
এটি মূলত বিহারের বাইরের অবস্থিত স্থাপনা। বিহারের দক্ষিণ দেয়াল হতে ২৭মি দক্ষিণে অবস্থিত একটি মঞ্চে অনেকগুলো স্নানাগার ও শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছিলো। মঞ্চটি পূর্ব-পশ্চিমে ৩২মি দীর্ঘ ও উত্তর-দক্ষিণে ৮.২৩ মি. প্রশস্ত। এটি বিহারের ১০২ নম্বর কক্ষ থেকে একটি উঁচু বাধানো পথ দ্বারা সংযুক্ত। এই পথের নিচে বিহার দেয়ালের সমান্তরালে ১.৯২মি চওড়া এবং ২.৫ মি. উঁচু একটি ভল্টযুক্ত খিলান রয়েছে। সম্ভবত বিহারের বহির্ভাগে অবাধে চলাচল এবং চারদিকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার জন্য এইরুপ করা হয়েছিলো।
সংলগ্ন স্থাপনাসমূহ :
স্নানঘাট
বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে প্রায় ৪৯মি দক্ষিণে প্রায় ৩.৫মি প্রশস্ত স্নানঘাট অবস্থিত। এর দুপাশে প্রতিটি দেয়াল ১.৫মি প্রশস্ত। খাড়াভাবে ইট স্থাপিত করে এ ঘাটটি নির্মাণ করা হয়েছিলো আর এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ধাপে বিরাটকার পাথর ছিল। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ঘাটটি ঢালু হয়ে প্রায় ১২ মি. নিচে নেমে গিয়েছে। ঘাটের উপর পুরু বালির স্তর ছিল। এ থেকে অনুমান করা হয়, এ ঘাট জলাশয় বিশেষতঃ নদীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল।
গন্ধেশ্বরী মন্দির
স্নানঘাট থেকে ১২ মি. পশ্চিমে পূর্বমুখী একটি ইমারত পাওয়া গেছে যাকে স্থানীয় ভাবে বলা হয় গন্ধেশ্বরীর মন্দির। এর দৈর্ঘ্য ৬.৭ মি. ও প্রস্থ ৩.৫ মি.। এর সম্মুখ দেয়ালের ইটে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মসহ বিভিন্ন ধরনের ফুলের নকশা এবং গাঁথুনিতে ব্যবহৃত উপাদান দেখে মনে হয় এদেশে মুসলমান যুগের প্রথম এ ইমারতটি নির্মিত হয়েছিলো। এতে একটি চতুষ্কোণ হলঘর রয়েছে। হলঘরের মধ্যবর্তী স্থানে অষ্টকোণাকৃতি একটি স্তম্ভের নিম্নাংশ পাওয়া যায়। পশ্চিমের উদগত একটি দেয়ালের বাইরের দিকে ১.৪ মি. বাহু বিশিষ্ট বর্গাকার একটি পূজার কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া হলঘরের চারটি কুলুঙ্গিতেও মূর্তি স্থাপনের ব্যবস্থা আছে।মন্দিরের সামনে একটি চত্বর আছে। এর মেঝে খাড়া ভাবে স্থাপিত ইট দিয়ে গাঁথা এবং গাঁথুনি পাহাড়পুরের অন্যান্য স্থাপত্য-নিদর্শন থেকে পৃথক।
জনপ্রিয় মাধ্যমে সোমপুর বিহার
সোমপুর বিহার নিয়ে বেশকিছু ভিডিও ডকুমেন্টারি নির্মাণ হয়েছে, ২০১৬ সালের ঈদুল আযাহায় চ্যানেল আই তে একটি বিশেষ টেলিফিল্ম রাজিব হাসান এর রচনা ও পরিচালনায় ''চাঁদের শহর'' প্রচার হয় যার সম্পূর্ণ গল্প ও চিত্রায়ন সোমপুর বিহারকে ঘিরে ।
পাহাড়পুর সংলগ্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত উল্লেখযোগ্য মূর্তি
বেলে পাথরের চামুণ্ডা মূর্তি
লাল পাথরের দণ্ডায়মান শীতলা মূর্তি
কৃষ্ণ পাথরের বিষ্ণুর খণ্ডাংশ
কৃষ্ণ পাথরের দণ্ডায়মান গণেশ
বেলে পাথরের কীর্তি মূর্তি
দুবলহাটির মহারাণীর তৈলচিত্র
হরগৌরীর ক্ষতিগ্রস্থ মূর্তি
কৃষ্ণ পাথরের লক্ষ্ণী নারায়ণের ভগ্ন মূর্তি
কৃষ্ণ পাথরের উমা মূর্তি
বেলে পাথরের গৌরী মূর্তি
বেলে পাথরের বিষ্ণু মূর্তি
নন্দী মূর্তি
কৃষ্ণ পাথরের বিষ্ণু মূর্তি
সূর্য মূর্তি
কৃষ্ণ পাথরের শিবলিঙ্গ
বেলে পাথরের মনসা মূর্তি