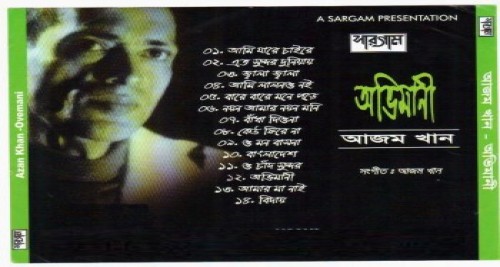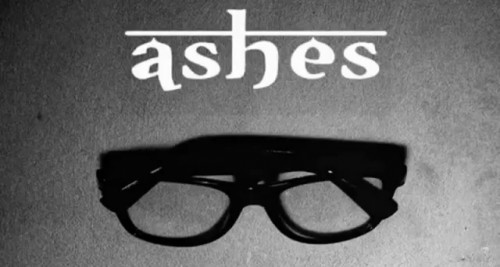প্রিয় লাল-সবুজ দেশটিকে বিদায় বলে অবিনাশী জগতে চলে গেছেন মুক্তিযোদ্ধা-ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান স্বাধীনতা পুরস্কারে প্রাপ্ত এই সংশপ্তক নারী মারা গেছেন গত ৬ মার্চ মঙ্গলবার। নির্যাতনে নুয়ে না পড়ে সৃজনশীলতার বাগানে ফুল ফোটানোর অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তিনি। গাছের শিকড়-বাকল, ডালপালা, কাঠের টুকরো ইত্যাদি ব্যবহারে তিনি গড়েছেন আশ্চর্য সব শিল্পকর্ম। কাঠের বুকে হাতুড়ি-বাটাল ঠুকে ভাস্কর্য রচনা করে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। একাত্তর নির্যাতিত এই বীরাঙ্গনার বয়ানে জাতি জেনেছে পাকিস্তানি হায়েনাদের লোলুপ বর্বরতার ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যদের ভয়াবহ ধর্ষণ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তিনিই একমাত্র জবানবন্দি-দানকারী। স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদানের জন্য ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে মুক্তিযোদ্ধা খেতাব দেয়। তার আগে ২০১০ সালে তিনি পান স্বাধীনতা পুরস্কার। যার জীবনের গল্প হার মানায় রূপকথাকেও। পাকিস্তানিদের নির্যাতন সম্পর্কে প্রথম কথা বলেন ২০০৯ সালে ডিসেম্বরে। জীবদ্দশায় তার ধানমণ্ডির বাসায় কথা হয়। কথপোকথনের কিছু অংশ প্রকাশিত হলো।
যেখানে জন্ম আর বেড়ে উঠেছেন, সেখান থেকেই শুরু করা যাক
আমার জন্ম নানাবাড়ি খুলনাতে। জন্ম তারিখ ১৯৪৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। বাড়িটির নাম ছিল ‘ফেয়ারী কুইন’ বা ‘পরীর রাণী’। আমার নানা অ্যাডভোকেট আব্দুল হাকিম ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের সরকারের সময় স্পিকার হয়েছিলেন। সারাক্ষণ ওই বাড়িতে লোকজনের ভিড় লেগে থাকত। আমার মায়ের নাম রওশন হাসিনা, তিনি ছিলেন পুরোপুরি গৃহিণী। বাবা সৈয়দ মাহবুবুল হক খুলনার দৌলতপুর কলেজে কমার্সের শিক্ষক ছিলেন। ভাইবোন মিলে আমরা ছিলাম পূর্ণাঙ্গ একটি ফুটবল টিম, মোট ১১ জন। আমি হচ্ছি সবার বড়। সবাই মিলে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে বড় হয়ে উঠি। পরে সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করায় নানাভাই ঢাকায় আসেন এবং আমাকেও তার সঙ্গে আসতে হয়। নানা মিন্টো রোডের বাসভবনে ওঠায় কাছাকাছি সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে ভর্তি হই। তখন শহীদ জাহানারা ইমাম ছিলেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। পরে অবশ্য খুলনায় ফিরে গিয়ে পাইওনিয়ার গার্লস স্কুল থেকে এসএসসি এবং খুলনা গার্লস কলেজ থেকে এইচএসসি ও ডিগ্রি পাস করি। কর্মজীবন শুরু করি শিক্ষিকা হিসেবে, ১৯৬৩ সালে খুলনার আগা খান স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করি।
আপনি সব সময় বলে থাকেন আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ১৯৭১ সাল, কেন এই বছরটি আপনার কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।
কেবল আমার জন্য নয়, বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয় গুরুত্বপূর্ণ বছর হলো ১৯৭১। কারণ লড়াই করে রক্ত বিলিয়ে ওই বছর আমরা পাই স্বাধীন ভূ-খণ্ড। মুক্তিযুদ্ধের এ বছরটি বাঙালির কাছে তাই আজীবন স্মরণীয়। যদিও ১৯৭১ আমার জন্য দুঃস্বপ্নের একটি বছর। ষোলো বছরের একটি কিশোরীকে ভুলের মাশুল দিতে হয় বছরের শুরুতেই, ভেঙে যায় আমার প্রথম সংসার। মানসিকভাবে আমি যখন বিপর্যস্ত ও বেদনাহত, তখনই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধের নয়টি মাস যে কেমন ছিল সেটা আমি কখনোই ভুলতে পারি না। আমি বুঝতে পারি না যে যুদ্ধ হবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সেনাবাহিনীর, কিন্তু এই সাধারণ বেসামরিক মানুষের ওপর যে পাকিস্তানি বাহিনীর ন্যক্কারজনক আচরণ এবং আক্রমণ, সেটা কেন? চোখের সামনে নারকীয় দৃশ্য। এখানে-সেখানে মা-বোনদের ধর্ষণ। কখনো গণধর্ষণ। নির্যাতনের শিকার নারীদের আর্তচিৎকার। আলোহীন প্রকোষ্ঠে প্রতিনিয়ত কতগুলো অসহায় নারীর মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া। হত্যাসহ সাধারণ মানুষের বাড়ি-ঘরে আগুন দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া-এসব কিছুই দেখেছি আমি।
আপনি একাত্তরে যে পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন, তা যদি খুলে বলতেন
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় টিকে থাকার প্রয়োজেনে আমি একটা মিলে চাকরি নিয়েছিলাম। প্রথম সংসারটি ভেঙে যাওয়ার পর ভেঙে না পড়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছি বলেই চাকরিটা নেই। চাকরির প্রয়োজনে খুলনায় আমি একাই থাকতাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার পরিবার আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ওরা আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কষ্টটা আমার বুকের মধ্যে থাকত তখন। মনে মনে ভাবতাম তারা কোথায় হারিয়ে গেল? আমি চাকরিজীবী তাই কোথাও যেতে পারলাম না। কিন্তু তারা গেল কোথায়? আমার তা জানা ছিল না। এ রকম একটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমার প্রথম তিনটা মাস গেল। ওইরকম একটা পরিস্থিতিতে মানুষ মনে করল আমি একা। সুতরাং চারদিকে যেভাবেই হোক খবর হয়ে গেল যে আমি ২৩ বছর বয়সের একটি মেয়ে ওই রকম প্রতিকূল অবস্থায়ও চাকরি করছি। সুযোগসন্ধানীরা আমার কাছে পাত্তা না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অবাঙালিরা সুযোগটা কাজে লাগাল।
পাকিস্তানি সৈন্য ধর্ষণ করছে, নারী নির্যাতন করছে- ওই অবস্থায় আপনি কম বয়সী একটি মেয়ে হয়ে খুলনা শহরে থাকার ঝুঁকি নিলেন?
অবিশ্বাস্য মনে হলেও ওইসব একেবারেই আমার কানে আসেনি। একা একা থাকতাম, লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা আর মেলামেশা কম করতাম। কেউ আমাকে সাবধান বা সতর্ক করেনি আর তখন তো মিডিয়া এ রকম জাগ্রত ছিল না, এত মিডিয়াও ছিল না। একটা টিভিও কারো বাসায় ছিল না। একটি টেলিফোন করতে হলে পিসিও (পাবলিক কল অফিস) থেকে করতে হতো। কল দিয়ে বহুক্ষণ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলতে হতো। সামনে যে আমার বিপদ, আমাকে কে টেলিফোন করে জানাবে? পরিস্থিতিটা তখন এমনই ছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিক থেকেই নারী নির্যাতন শুরু হলেও সেন্সরশিপের কারণে পত্র-পত্রিকায় ওসব আসেনি। আর ওই সময় তেমন কারো সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না। সারাদেশে যে কী চলছে, বোঝার কোনো উপায় নাই। মনে হয় যেন আমি একাই বোধহয় এ রকম নির্যাতিত হয়ে চলছি। সারাদেশে যে নারী নির্যাতনের বিষয়টি উত্তাল হয়ে পড়েছে তা বুঝতে পারিনি এবং ওই বয়সে বুঝতামও না যে, নারী নির্যাতন কী। সংসার ও স্বামীর সঙ্গে গণ্ডগোল তখনই সেটা সামাল দিব, না নির্যাতিত যে হচ্ছি সেটা সামাল দিব? আসলে কোনটা যে নারী নির্যাতন তা’ বুঝে উঠতে পারছিলাম না। নির্যাতনকেই স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিয়ে নির্যাতিত হয়েছি।
প্রথম নির্যাতনের পরে কী আপনি মিল থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করেছেন বা করতেন?
চেষ্টা তো করেছি কিন্তু পারিনি। কারণ একদিকে আমার চাকরি, ওভারটাইম, বেতন। মাকে মাসে মাসে টাকা পাঠানো। নিজের বাচ্চাদের টাকা পাঠানো। এসবের জন্য বের হতে পারিনি। তারা ছিল যশোরের আশ্রয় কেন্দ্রে। তাদের বাঁচানো আমার দায়িত্ব।
স্বাধীনতার পর কী পরিস্থিতিতে পড়লেন?
একাত্তরে আমি পেয়েছি দৈহিক যন্ত্রণা, শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছি। আর স্বাধীনতার পর স্বাধীন দেশে পেয়েছি মানসিক যন্ত্রণা। দীর্ঘ সময় একাই পথ পাড়ি দিতে হয়েছে আমাকে। মা প্রগতিশীল এবং ভাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও যুদ্ধ শেষ হলে অনেকটাই একা হয়ে পড়ি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেক গঞ্জনা, অপবাদ সইতে হয়েছে আমাকে। আমি একটা খারাপ মেয়ে, আমি চরিত্রহীন- সবাই তাই মনে করত। এরই মধ্যে একসময় আমি আবিষ্কার করলাম দুই মাসের না তিনমাসের কনসিভ। সাংঘাতিক বিপজ্জনক পরিস্থিতি! জানি না কে? কার দ্বারা? কী রকম ভয়ঙ্কর। মাথার ঘায়ে কুকুর যেমন পাগল হয়ে দৌড়ে বেড়ায়। আমিও তেমন ঘরের মধ্যে ছিলাম আর বলছিলাম আল্লাহ আমাকে বাঁচাও। আল্লাহ আমাকে বাঁচাও। আমি কার কাছে যাব? এমআরের আমি টাকা কোথায় পাব?
আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। আমি কোথায় পাব টাকা? তখন এমআর করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করছি। শেষে সুদে ৫০০ টাকা জোগাড় করে এমআর করাই। একাত্তরের পরের বছরগুলোতে বুকের মধ্যে উত্তাল যন্ত্রণার ঢেউ আছড়ে পড়ছিল, কখনো সবার আড়ালে নিজের একান্ত প্রান্তে এসে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছি। খুঁজে ফিরেছি সামাজিকভাবে আমার বারবার অসম্মানিত হওয়ার সঠিক কারণগুলো। উত্তর সহজেই মিলেছিল। স্বাধীনতার মহান যুদ্ধের আমি পলে পলে সাক্ষী। নয়টি মাসের কলংক মুছে ফেলে আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। অসাড় সমাজকে প্রবল আঘাতে প্রত্যাখ্যান করে মহান স্বাধীনতার মূল্যবোধে নির্মাণ করতে সচেষ্ট ছিলাম। আমার সৃজনে সান্ত¡না, মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত চেতনা আমার বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। এখন আমার মনে হয়, এই যুদ্ধে আমরা যারা অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছি, তাদের সবারই পুনর্জš§ লাভ হয়েছে। আমি তখন ২৩ বছরের তরুণী। তিন সন্তানের জননী। ঘর-গৃহস্থালি আর একটি জুট মিলে চাকরি করি। রাজনৈতিক পরিবারে থাকলেও আমি এসবের কিছুই বুঝতাম না। মা রওশন আরার কাছে যেটুকু শুনতে পেতাম সেটুকুই আমরা রাজনৈতিক জ্ঞান। তবে স্বদেশের প্রতি যে ভালোবাসা সেটা অকথিত ভাষা, যা আমার প্রাণেমনে সঞ্চিত চিরজাগ্রত। আজ স্বাধীন বাংলাদেশে স্কুলের শিশুরা গান করে আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। ভাবতে বুকটা আনন্দে ভরে ওঠে। আমরা স্বাধীন বাংলার গান গাইছি। ৩০ লাখ মানুষের আত্মদানে হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সূর্যোদয়।
বীরাঙ্গনা কি মূল্যায়ন বা সম্মান পাচ্ছে?
না মূল্যায়ন পাচ্ছে না। আমি অন্তত দেখিনি কাউকে মূল্যায়ন করতে। কয়েকজন ভালো গৃহিণীকে আমি চিনি। তাদের সঙ্গে যুদ্ধের পরে এয়ারপোর্টে আমার দেখা হয়েছিল। তারা আমার কাছে বিশেষভাবে রিকোয়েস্ট করেছে আমি যেন তাদের নামটা না বলি। সুতরাং আমি কথা দিয়েছি যে আমি জীবনেও বলব না। তাই এখনো বলিনি আমি যা হারিয়েছি তা কোনোদিনও পূরণ হবে না। ইতিহাসেও সেই অপূর্ণতা থেকে যাবে। তবে সবার কথা জানি না, আকস্মিক হোক আর যেভাবেই হোক সৌভাগ্যবশত সামগ্রিকভাবে সমস্ত সমাজ আমার অভিমান ভাঙাতে পেরেছে। যেহেতু আমি কারো কাছে কোনো প্রতিদান চাই না তাই কষ্ট পাই কম। প্রতিদান যদি চাইতাম তাহলে অনেক কষ্ট বাড়ত। প্রতিদান না চাওয়ার ফলে একটা জিনিস হয় যেমনটা সবসময় শান্তই থাকে। বিক্ষিপ্ত হয় না যে আমাকে ওটা দিল না বা কেউ এটা বলা উচিত ছিল বলল না। কারো কাছে কিছু না চাওয়ার মতো শান্তি আর কিছু নাই।